নরেন্দ্রনাথের প্রায় চারশো গল্পের অজস্র চরিত্রের বিপরীতে তাঁর কাঁচামাল ততবেশি নয়। এই বিপুল গল্পের সমাহার তিনি গড়ে তুলেছেন কলকাতার সাধারণ সমাজজীবনের অপরিহার্য কিছু অনুষঙ্গ দিয়ে। তার গল্পমালা সকালের বাজার, অফিসের কেরানি, ট্রামে ঝোলা, কলেজ ফেরত তরুণী দেবর-বউদি-ওগো-হ্যাগো ইত্যাদি কিছু নিয়মিত টুলের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। খোলামাঠের শুকনো পাতার মতো ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলানো হৃদয়, দু-তিনটি চিঠি আর কয়েকটি হাহাকারের পাঁচফোড়ন সহযোগে পরিবেশিত হয়ে থাকে।
এইসব সাধারণ যাপিত জীবনের সুখ-দুখ সবকালে জনপ্রিয়, তার উপর নরেন্দ্রনাথ লিখেছেন এমন একটা সময়ে যখন এখনকার মতো ম্যাগাজিনগুলোকে অস্তিত্বের সংকটে ভুগে নানাবিধ হিসেব নিকেশ করতে হতো না। বৈশ্বিক সাহিত্যের অজস্র প্রবাহের জোগান না থাকায় তুলনা করার মতো প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে সেসব পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিল এখনের চেয়ে কম আয়াসে। সাগরময় ঘোষ লিখেছেন, পূজোকালীন সময়ে এমনও হয়েছে লোকে ছুটি কাটাচ্ছে আনন্দ করছে আর নরেন্দ্রনাথ পাল্লা দিয়ে গল্প লিখে চলেছেন আগামীকালের পত্রিকার জন্য। এহেন ছুটে চলা, আর কাউকে ফিরিয়ে দিতে না পারা লেখকের সাথে যদি আবার পাল্লা জুড়ে দেওয়া হয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো লেখককে, তখন রাশি রাশি না লিখে উপায়!

লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র
অবশ্য নরেন্দ্রনাথ তার সহজাত প্রতিভার গুণে যা লিখেছেন তাতেই রসসৃষ্টি করেছেন। কোনো না কোনো মাত্রায় সে লেখা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তাই তো সন্তোষকুমার ঘোষ উচ্চারণ করেছিলেন, ‘গল্পকে গল্প করে বলা, সেইসঙ্গে শিল্পের স্বচ্ছতম গুনটিকে ঘাসের শীষে শিশিরবিন্দুর মতো ধরে রাখা—নরেন্দ্রর জোর বলুন জাদুশক্তি বলুন সব এইখানে। আর অনায়াস তাঁর এই সিদ্ধি। সেখানে তিনি মঁপাসা, ও’ হেনরি, শেখভ কি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ আসনে।’
তবু সব লেখকেরই তো সীমানা থাকে। অনেকসময় আপন যোগ্যতাগুলোই নিজেকে একটি সীমানায় বেঁধে ফেলে সৃষ্টিকে তুলনা করবার সুযোগ করে দেয়। নরেন্দ্রনাথের ‘শিল্পের শিশিরবিন্দুকে গল্পের শীষে’ ধরে রাখার কৌশলের কারণে সব লেখাই হয়তো একটি নিজস্ব স্ট্যান্ডার্ড ধরে রাখে। কিন্তু কিছু কিছু লেখা সাধারণের তালিকা থেকে একপায়ে উঁচু হয়ে দাঁড়াতে চায়, কালের বহুদূর সীমানা থেকে যা একজন লেখকের সৃষ্টির সীমানা নির্ধারণ করে। এইসব একস্ট্রা অর্ডিনারি, ঘাড় উঁচু করে থাকা রচনাগুলোই কালের বিচারে লেখককে পাঠকের মাঝে ধরে রাখে।
‘রস’ নিয়ে অজস্র কথা হয়েছে, ‘বিকল্প’কে আবু সয়ীদ আইয়ুব বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বড় গল্পের পর্যায়ে উন্নীত বলেছেন, ‘সেতারে’র বিষয়ে জাকির তালুকদার শ্রেষ্ঠগল্পের ভূমিকায় লিখেছেন—‘পুরুষতান্ত্রিক মনোজটিলতার এক নিখুঁত চালচিত্র’। আমি সেসব পুনরায় বলে বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। এই সন্ধ্যায় আমি কেবল দুটি গল্পের কথা বলে এই ঝাঁপ নামিয়ে রাখব।
তার অন্যসব প্রেমের গল্পের থেকে আলাদা একটি রচনা হলো ‘দ্বিচারিণী’ রচনাটি। দুটি হার্দিক সম্পর্কের বাঁধনে যুক্ত পরিবারের মাঝে কেমন করে ফুলেফেঁপে ওঠে হিংসা, কী করে সামান্য কারণে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, মানুষের মাঝে ভালো দেখানোর জন্য কীরকম মেকি ভাব ধরতে পারে তার নিদারুণ শব্দচিত্র এঁকেছেন তিনি। আবার অকর্ষিত বুদ্ধির একজনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার ফল যে আখেরে ভাল আসে না, জীবনে চলার পথে অযথা হোঁচট খেতে হয় তারও তুলনা করেছেন এখানে। এইসব নানান বিচারে এই রচনাটি আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।
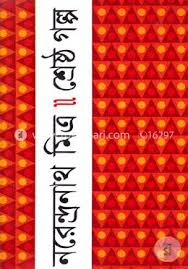
প্রচ্ছদ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র ।। শ্রেষ্ঠ গল্প
অন্য যে লেখাটির স্মরণ করতে চাই সেটি হচ্ছে ‘ছোট দিদিমণি।’ ধনী আর দরিদ্রের চিরকালীন বিভেদের গল্প এটি। নিয়ত দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এক পরিবারে কিঞ্চিত সুখের আশায় গৃহকর্ত্রী স্কুলের চাকরি নেন। সেখানের শিক্ষিত ধনী পরিবারের মেধাবী শিশু আর নিজের আপাত অমনোযোগী শিশুদের তুলনা করে ভাবতে বসেন, মেধা-বুদ্ধিও কি তবে ওই ধনের সাথেই বাঁধা। মেধাবী শিশুদের সাথে মিলেমিশে নিজের সন্তানটিও বিদ্যায়-গুণে উত্তম হয়ে উঠুক এই কামনায় মা নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে যেচে ধনীদের সাথে বন্ধুত্ব করেন। তাদের মনভুলোনো কথা, শ্লেষ ইত্যাদি গায়ে মেখে নিয়েও যখন দেখেন প্রকৃতির অনিবার্যতায় কীভাবে যেন ধনী আলাদাই থাকছে, শ্রেষ্ঠত্বর মুকুট তার গলায়ই পড়ছে বারবার তখন সব আশার বেলুন ফুটো হয়ে যাওয়া মায়ের সামনে একটি পথই খোলা থাকে—মেনে নেওয়া। কিন্তু সেখানেও বিপদ, ওপরতলার মানুষেরা দরোজায় খিল এঁটে বুঝিয়ে দেয় তুমি আমাদের নও, আমাদের মতো নও। সেই বেদনার তুলনা করবার মতো শক্তি, এবং তাকে ভাষায় প্রাণ দেবার ক্ষমতা আছে বলেই নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্প এখনো পাঠকের টেবিলে রয়েছে।
সাধারণ এসব দুঃখবেদনা ক্ষুদ্র কিছু প্রাপ্তি নিয়ে রচিত এইসব গল্পমালা এখনো যাপিত জীবনে আলোড়ন তুলছে, পাঠে চর্চিত হচ্ছে, মানুষকে বলছে এইসব দিনরাত্রির কথা।


