বই : শবনম
লেখক : সৈয়দ মুজতবা আলী
প্রকাশক : স্টুডেন্ট ওয়েজ, কলকাতা
প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০
হিমের প্রতাপ, কুয়াশার ইন্দ্রজাল, শতরঙের কুমার ফুলের সম্মিলনে শীতের পুষ্পস্তবক। পুষ্পে পুষ্পে আলোক চুম্বিত শিশিরবিন্দু, ভ্রমর, মৌমাছি, প্রজাপতি এবং বুলবুলের চপল ওড়াউড়ি–পরজনের প্রণয় চলচ্চিত্রে পার্শ্বনায়কের ভূমিকায় গত হওয়া কুমারত্বের যৌবনকাল। একটি শিশিরবিন্দু, কৃষ্ণ ভ্রমর, মধুরানি মৌমাছি কিংবা পুষ্পশখী বুলবুল–আমার সঞ্চিত কুমারত্ব তাদের শিহরন-জাগানিয়া স্পর্শ পায়নি কখনও। অবশ্য অঘোষিত নিশেধাজ্ঞায় আমার কুমারাঞ্চলে তাদের প্রবেশই ছিল নিষিদ্ধ। কারণ সে সংরক্ষিত অঞ্চল সূদুর হিন্দুকুশের তুষার মুকুট ছুঁয়ে আসা এক ফোঁটা শিশিরের জন্যে নির্ধারিত–যার প্রেমময় নাম শবনম।
কাব্য, কাব্যের ভাব এবং বুঝ—কাব্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি স্বঘোষিত ত্বিফলে মক্তব। এতদ্বসত্বেও কোনো রচনা যখন আমাকে এমন পদ্যাভ গদ্য রচনায় প্ররোচিত করে, তখন সে রচনার সমীহস্তুতি গাইতেই হয়।
সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলায় গুরুগম্ভীর সাহিত্য রচনাকারীদের অন্যতম একজন। আমার মতে এ ধরনের গুরুগম্ভীর সাহিত্য রচনার পেছনে তাঁর শিক্ষাগত গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্বই বহুলাংশে দায়ি। একাডেমিক জীবনে পিএইচডির ফিরিস্তি বহু ভাষায় ব্যুৎপত্তি এবং অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জীবন তাঁকে আপন রচনায় সহজ হতে দেয়নি কিংবা পাণ্ডিত্যের দায়ে নিজেই হয়তো সহজ হতে চাননি। ফলে তাঁর যাবতীয় রচনাই পাঠকের পাঠ-গতিকে হ্রাস করে শম্বুকীয় পর্যায়ে নিয়ে আসবার মতো শক্ত।

সৈয়দ মুজতবা আলী
কিন্তু কোনো সৃষ্টিশীল রচনাকে সহজ-তরল এবং শক্তের মানদণ্ডে বিচার করে পাঠ্য-অপাঠ্যের তালিকা করা একজন মননশীল পাঠকের জন্যে কোনোভাবেই স্বাস্থ্যকর নয়। তবুও একটা সময় আমি যখন হুমায়ূনীয় কথা সাহিত্যের তারল্যে মোহগ্রস্ত ছিলাম, তখন এই তারল্যের মানদণ্ডেইই পাঠ্য এবং অপাঠ্যের বিচার করতাম। পাঠ-তালিকা তৈরি করতাম।
সাহিত্য—রুচির বাল্যকালের সে সময়টাতে এক সাহিত্য-গুরুর পরামর্শে হাতে নিয়েছিলাম সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘দেশে বিদেশে’। আমার প্রিয় জনরা–ভ্রমণবৃত্তান্ত সঙ্গে আফগান এবং পাঠানকাহিনি সব মিলে পাঠকচৈতন্যকে আকৃষ্ট করবার মতো দুর্দান্ত একখানা পুস্তক। কিন্তু আমার তরলভক্ত সাহিত্যরুচি মুজতবার ধাতব বর্ণনাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারেনি। ফলাফল—অসমাপ্ত দেশ বিদেশ। সেবার মুজতবা আলীর সঙ্গে দেশ-বিদেশের যাত্রায় বেশিদূর যেতে না পারলেও এ পণ্ডিত আদমিকে আমার মনে ধরেছিল। অবশ্য এর অন্তর্নিহিত কারণ ছিল তিনটি। এক–বইয়ের ফ্ল্যাপে স্থুলো মানুষটির পাণ্ডিত্যের ফিরিস্তি। দুই–সাহিত্যগুরুর পরামর্শ। তিন–তাঁর রচনায় গাম্ভীর্য এবং রসবোধের এক অদ্ভুত এবং আকর্ষণীয় মিশেলের উপস্থিতি।
গবেষণামূলক রচনার ক্ষেত্রে যদিও আমি সরল-শক্তে ভেদ করিনি কোনোকালে, বরং এমন রচনার ক্ষেত্রে মূল বার্তা বুঝে আসাটাই ছিল মূখ্য। কিন্তু কথাসাহিত্যের মৌলিক বিভাগসমূহ–গদ্য গল্প এবং উপন্যাসে আমি বরাবরই সরল সাহিত্যে স্বচ্ছন্দে ছিলাম। কিন্তু তরল সাহিত্যে অভ্যস্ত সাহিত্য–রুচির বদান্যতায় যখন কঠিন এবং গম্ভীর সাহিত্যে অলংকৃত, ভাষার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠায় উন্নীত বিভিন্ন রচনা থেকে বঞ্চিত হতে থাকলাম, তখন এ রুচির বলয় ভেঙে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতে শুরু করলাম। বলয় ভাঙার প্রচেষ্টার সিলসিলাতেই পাঠ করলাম সৈয়দ মুজতবা আলীর শবনম।
সুদূর পাথুরে আফগান ভূমির পাগমান কান্দাহার কাবুল মাজার ই শরীফের আব এবং হাওয়ায় ভেসে ভেসে, হিন্দুকুশের চূড়ান্ত শিখরে স্থাপিত শুভ্র তুষার মুকুট ছুঁয়ে আসা শবনম। তুর্কি রক্ত কণিকায় সঞ্জীবিত, আফগান হাওয়া বাতাসে সভ্য-ভব্য, চপল এবং ইউরোপীয় সভ্যতার মাতাল ঘ্রাণে উচ্ছল- চঞ্চল শবনম।
কাব্যবিলাসিনী এ রমণী যখন আশৈশব বাংলার নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় পলিমাটির অস্তিত্ব নিয়ে বেড়ে ওঠা এবং আফগান শুষ্ক বাতাসে শুকনো খরখরে ঝুড়া মাটিতে পরিণত হওয়া মজনুনের জীবন-চলচ্চিত্রে প্রবেশ করে, তখন মজনুনকে আক্ষরিক অর্থেই মজনুন মনে হয়। দৃশ্যটি হয়ে ওঠে গভীর সমুদ্রে অপেক্ষমাণ ঝিনুকের কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি–বিন্দু পেয়ে যাবার মতোই প্রীতিকর। অস্পৃশ্য কিছুকে পরমস্পর্শ পাবার বাসনায় মজনুনের কালো-সাদা জীবন–ক্যানভাস রূপান্তরিত হয় মডার্ন কোনো পিকাসোর কোটি ডলারের রঙিন পেইন্টিংয়ে। শুরু হয় মানব-মানবীর আদিম রসায়নের মনন পর্ব।
প্রেম প্রেম আলাপনগুচ্ছের সূত্র ধরে এগিয়ে যেতে থাকে এই মনন পর্বটি। এ পর্বটি অন্যান্য মিডল ক্লাস গল্প-উপন্যাসের অতি সাধারণ ন্যাকামোপূর্ণ মনন পর্বের মতো হলেও মূলত লেখক এ পর্বটিতেই তার পাণ্ডিত্যের ঝলক সবচেয়ে বেশি দেখিয়েছেন। মহাকবি হাফিজ আধ্যাত্মিক রুমি, কখনও বা স্বরচিত খণ্ড খণ্ড কাব্যালংকারে ঢেকে দিয়েছেন মনন পর্বের সাধারণ কায়া। রূপান্তরিত করেছেন আপন কল্পনায় স্বেচ্ছাচারী বাধাহীন শিল্পীর আঁকা প্রেমময় যাবতীয় গল্প–চিত্রের ক্যানভাস ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলা এক প্রেম–চিত্র; যে চিত্র দেখলে মনের কৃষ্ণ গহ্বরে সে পথে পা বাড়াবার নিষিদ্ধ কামনার উদ্গীরণ শুরু হয়—যে পথে পা রাখবার দুঃসাহ দূরে থাক সাহসই হয়নি কখনও।
কাব্যের ঝংকার, মেটাফরের উপযুক্ত প্রয়োগ এবং অসংখ্য অজানা শব্দের ব্যবহার–কাব্যের পাঠশালায় নিতান্তই শিশুটির কাছে উচ্চাঙ্গীয় সাহিত্যের এতসব উৎকৃষ্ট উপাদান বোঝাই বটে। তাই লেখক যখন উপর্যুপরি কাব্যের ব্যবহার এবং অদেখা শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকেন তখন আমার পাঠকসত্তাটি নিতান্তই হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু হতাশার প্ররোচনায় অসমাপ্ত গ্রন্থের বোঝা ভারী করবার চে অবোধ্য কাব্য এবং অপরিচিত শব্দের বোঝা বহন করাকে শ্রেয় মনে করে পুনর্পাঠে লিপ্ত হই। বিশাল উল্লম্ফন দেওয়ার আগে কয়েক পা পিছিয়ে আসবার মতো করে শেষ স্টপেজের খানিকটা আগ থেকে যখন পুনর্পাঠ শুরু করি, তখন আমার পাঠকসত্তা অভিভূত হয়ে পড়ে। কাব্য–খণ্ডলোকে মনে হয় গদ্যের পদ্ম। আর অদেখা শব্দসমূহের সমষ্টি রূপান্তরিত হয় একেকটি শব্দস্তবকে।
এভাবেই আমি এগিয়ে যাই পাপ–স্পর্শ বঞ্চনার সৌভাগ্যে মোড়ানো দুটি মানব মানবীর মনন-রসায়নের প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনা থেকে সমাপ্তিতে। মাঝে আমি অবলোকন করি—তীব্র শীতে তুষারের সফেদ চাদরে জড়ানো জুবুথুবু আফগানিস্তান, অসর্পিল কাবুল নদী, হিন্দুকুশের দিগন্তবিস্তৃত প্রাচীর, কাবুল কান্দাহারসহ আফগান নগরীগুলোতে জমজমাট হয়ে ওঠা ক্ষমতার লড়াই। একদিকে ইউরোপের মানসপুত্র বাদশা আমানুল্লাহ আরেকদিকে প্রস্তর কঠিন বাচ্চায়েস্কাওয়ের ডাকু দল। দ্রিম দ্রিম ঠুশ ঠাশ! বাতাসে বিপজ্জনক তপ্ত সিসা খণ্ডের ওড়াউড়ি। যুদ্ধের প্রাণঘাতী স্বভাবের ফলে বিরান পথঘাটে আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা নারী অবয়ব দূরে থাক কোর্তাওয়ালা সুঠাম দেহী কোন পাঠানের টিকিটিও নেই সেখানে। এমন অঘোষিত কারফিউর মাঝেই হঠাৎ কোনো এক গলির মাথায় একটি অবয়বের উদয় হয়। তার হাঁটার রোখ বাঙালি মাষ্টারের আবাসস্থলের দিকে। মাথায় সমূহ বিপদের পরোয়ানা। পদে পদে ওঁত পেতে থাকা ডাকু দল। ডাকুদের সেনাপতি জাফরের অপবিত্র কামনার খড়গ। তবে কি বাচ্চায়েস্কাওয়ের ডাকুদের হাতে বন্দি হয়ে সেনাপতি জাফরের অপবিত্র কামনার বলি হবে এ হতভাগিনী? নাকি তার মনের রাজপুত্রের সমীপে নিজের সর্বকাঙ্ক্ষিত সত্তাকে ঈর্ষণীয় সমর্পণের মাধ্যমে নারীপ্রধান উপাখ্যানকে নর-শ্রেষ্ঠত্বের চিরসত্য রঙে রাঙিয়ে দিবে? উত্তর ফাঁস করে স্পয়লার দিব না বরং উত্তর খোঁজবার দায়িত্ব পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি।
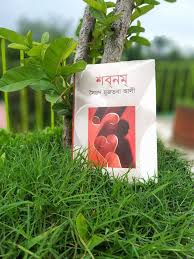
নতুন মোড়কে শবনম
গম্ভীর ভাষায় রচিত সৈয়দ মুজতবার এই গভীর রচনা আমাকে উপহার দিয়েছে অনেক দুর্বোধ্য শব্দসমারহে সজ্জিত শব্দস্তবক–যে শব্দস্তবকের শব্দসমূহের অর্থোদ্ধারে আমাকে ঝক্কি পোহাতে হয়েছে বেশ। কতক শব্দের অর্থ তো অদ্যাবধি উদ্ধার হয়নি। আমার অভিধানে যুক্ত এসব বোবা শব্দ আমার শব্দ–দৈন্যতার ঘোষণা দিয়েছে নিশ্চয়। আমিও এই ঘোষণা নির্দ্বিধ কণ্ঠে কবুল করি। কিন্তু এ শব্দ–দুর্বলতা ছাপিয়ে যে বিষয়টিকে আমার পাঠকসত্তা অস্বস্তিকর হিসেবে চিহ্নিত করেছে–কথাসাহিত্যের অমন গুরুগম্ভীর স্টাইল। লেখক মহোদয় প্রতিটি প্যারায় প্যারায় পাণ্ডিত্যের ঝলক সৃষ্টি করেছেন–যে ঝলকানির মাঝে লীন হয়ে গেছে একটি কোমল গল্পের কুসমিত আলো। উচ্চাঙ্গীয় সাহিত্যের বহিঃপ্রকাশের কামনায় হারিয়ে গেছে কথাসাহিত্যের সরল ধারাটি।
পাঠক ভাবতে পারেন–এসবই হুমায়ুনীয় তরল সাহিত্যে অভ্যস্ত একটি অপরিপক্ব পাঠক মস্তিষ্ক থেকে উৎসারিত কতক অবান্তর আপত্তি। আমি পাঠকবর্গের এমন অভিযোগ সবিনয়ে গ্রহণ করি। সৈয়দ মুজতবার সাহিত্য চর্চার কাল ও তৎকালীন কথাসাহিত্যের রংঢং ভার্সেস হুমায়ুনের সাহিত্য চর্চার কাল ও বর্তমানের কথাসাহিত্যের ফ্রি স্টাইল–এমন তুলনামূলক বিশ্লেষণে পাঠকের মনে যদি কোনো অনুযোগের সৃষ্টি হয় তবে বিতর্কের খাতিরে আমি তাদের অনুযোগের যৌক্তিকতাও স্বীকার করি।
অবশ্য কারুর সঙ্গে বিতর্কে জড়ানো আমার উদ্দেশ্য নয় বরং বিতর্কের মাধ্যমে বাংলা কথাসাহিত্যের স্বতন্ত্র দুটি ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠবার মাধ্যমে বাংলাভাষার যে সমৃদ্ধি ফুটে উঠবে সেটা পাঠকের সামনে তুলে ধরাই আমার মনজিলে মকসুদ। সুতরাং পাঠকের যাবতীয় অভিযোগ-অনুযোগ কবুল করবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এ কথাও বলি–হুমায়ুন তার সাহিত্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিরাট একটি পাঠকশ্রেণির মানসে কথাসাহিত্যের যে ফ্রি স্টাইল স্টাবলিশ করেছেন এবং কালের মানদণ্ডে উন্নীত করে গেছেন–সে ফ্রি স্টাইল বা সরল ধারা তার আগে পাঠক সমাজে অতটা আপন ছিল না। তখন মুহুর্মুহু নয়া শব্দ, দুর্ভেদ্য ম্যাটাফোর পঞ্চান্ন বগির রেলের মতো লম্বা লম্বা বাক্যই ছিল কথাসাহিত্যের মানদণ্ডে উন্নীত হবার সুষম উপকরণ। গদ্য গল্প উপন্যাস কথাসাহিত্যের প্রতিটি শাখাতেই ছিল এসব উপকরণের উপচে পড়া ভীড়। কিন্তু মানব স্বভাব তো সর্বদাই সহুলাত-পসন্দ, তাই ওসব রচনায় একটা নবাবি গাম্ভীর্য থাকলেও কালক্রমে মানুষ আধুনিক কথাসাহিত্যের সরলতাকেই অভ্যর্থনা জানিয়েছে। তাই সেকালের রচনাসমূহ নবাবি স্টাইলে বাংলাসাহিত্যের একটি বিস্তীর্ণ কাল শাসন করলেও বর্তমান অধুনা সময়ের রাজা কথাসাহিত্যের সরল রচনাসমূহই। সুতরাং কথাসাহিত্যে আদি ধারাটির এন্টিক মূল্য থাকলেও বর্তমানে সাহিত্যের আইডল হয়ে উঠবার জন্যে একজন লেখককে আধুনিক ধারাটিই নির্বাচন করতে হবে।
দিন কতক আগে অনলাইন এক্টিভিস্ট ফাহাম আবদুস সালাম বাংলাকে একটি দেউলিয়া ভাষা আখ্যায়িত করবার মনস্কামনা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একখানা পোস্ট করেছিলেন। পোস্টটি পড়বার পর আমার মনে হয়েছিল–শুধুমাত্র সেবা প্রকাশনীর বই পড়ে সেই শৈশবে বাংলা সম্পর্কে আমার মনে যতটুকু ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল বাংলা সম্পর্কে ফাহাম সাহেবের ফাহাম তার চে অনেক কম। তার দার্শনিক সুলভ বিভিন্ন যুক্তি খাড়া করে বক্তব্য প্রতিষ্ঠার কোশিশ দেখে আমার আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছিল–তিনি বাংলাকে একাডেমিক বোঝাপড়া বা শাস্ত্র বিশ্লেষণের মানদণ্ডে মেপেছেন। ফলে বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা এবং শাস্ত্র বিশ্লেষণের ক্রমবর্ধমান স্বাতন্ত্র্য তার সামনে অদৃশ্যই থেকে গেছে। তিনি এ বাস্তবতাও হয়তোবা ভুলে বসেছিলেন–কোনো নির্দিষ্ট জাতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র যখন দীর্ঘ একটি সময় সে জাতি এবং তাদের ভাষার মাধ্যমেই চর্চিত হয়, লালিত-পালিত হয়, তখন শাস্ত্রটির পরিভাষা বা এস্তেলাহ এবং উসুল সে ভাষাটির অনূকূলেই গড়ে উঠে। ফলে অপর আরেকটি ভাষার মাধ্যমে—যদিও সে ভাষাটি শাস্ত্রের মূল ভাষার চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় হয়, তবুও সে শাস্ত্রের এস্তেলাহ এবং উসুলকে পরিপূর্ণ আবেদন নিয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে না। ফলে পাঠকবর্গ যখন ভীনদেশি ভাষার কোনো শাস্ত্র নিজ ভাষায় অনূদিত হবার পর তা পড়তে বসবেন, তখন সে শাস্ত্রের প্রকৃত রূপ-রস আস্বাদন করতে পারবেন না।
উদাহরণ হিসেবে আরবে এবং আরবিতে চর্চিত ফিকহ শাস্ত্রের কথাই ধরা যাক। পৃথিবীতে প্রায় ৩৭০ মিলিয়ন মানুষ ইংরেজি ভাষায় কথা বলে। এখন যদি ফিকহের কোনো একটি মাসয়ালা (সমাধানযোগ্য উদ্ভূত সমস্যা) উসূল (শাস্ত্রীয় মূলনীতি) এবং এস্তেলাহের (শাস্ত্রীয় পরিভাষা) আলোকে ইংরেজিতে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে আরবিতে বিশ্লেষণ করলে বিষয়টির যে আবেদন তৈরি হতো সেটি ইংরেজিতে করবার কারণে হয়নি বরং অনেক ক্ষেত্রে অস্পটতা থেকে গেছে। ঠিক একই ঘটনা ঘটবে কেবলই ইংরেজিতে চর্চিত কোনো শাস্ত্রের আরবি কিংবা বাংলা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। কিন্তু নিয়মিত চর্চিত হলে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট ভাষা নির্ভরতা কমে আসবে এবং নির্দিষ্ট ভাষার বলয় ভেঙে তা অন্যান্য ভাষাতেও সহজবোধ্য হয়ে উঠবে। সুতরাং ভাষার স্বভাবজাত এ সীমাবদ্ধতার দরুন কোনো ভাষাকে দেউলিয়া ঘোষণা করলে একই যুক্তিতে পৃথিবীর সকল ভাষাকেই মিসকিন বলতে হবে। আর ইতোমধ্যেই বাংলা সাহিত্যের সীমিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা কথাসাহিত্যের দুটি স্বতন্ত্র ধারা সাব্যস্ত করে আমাদের ভাষার প্রাচুর্য প্রমাণ করে এসেছি। সুতরাং সকল ভাষাকে মিসকিন না বলে কেবল বাংলাকে মিসকিন বললে তা আন্যায়ই হবে বৈকি।
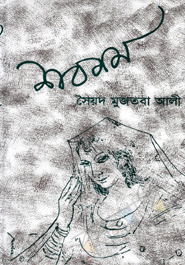
প্রচ্ছদ : শবনম


