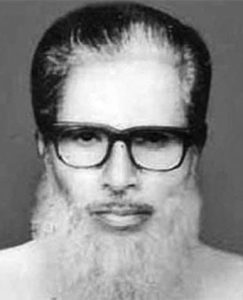 মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪) সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ১৩০৩ বঙ্গাব্দের (১৮৯৬) ২৮ ভাদ্র সাতক্ষীরা জেলার বাঁশদহ গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা মুনশি মোহাম্মদ ইব্রাহিম ছিলেন একজন পল্লিচিকিৎসক। তাঁর ডাক্তারখানায় সংবাদপত্র পাঠ ও নানা বিষয়ে বিতর্ক চলত। এসব বিষয় কিশোর ওয়াজেদ আলীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এ থেকেই ভবিষ্যৎ জীবনে একজন সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন তাঁর মধ্যে দৃঢ়মূল হয়।
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪) সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ১৩০৩ বঙ্গাব্দের (১৮৯৬) ২৮ ভাদ্র সাতক্ষীরা জেলার বাঁশদহ গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা মুনশি মোহাম্মদ ইব্রাহিম ছিলেন একজন পল্লিচিকিৎসক। তাঁর ডাক্তারখানায় সংবাদপত্র পাঠ ও নানা বিষয়ে বিতর্ক চলত। এসব বিষয় কিশোর ওয়াজেদ আলীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এ থেকেই ভবিষ্যৎ জীবনে একজন সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন তাঁর মধ্যে দৃঢ়মূল হয়।
ওয়াজেদ আলীর শিক্ষাজীবন শুরু হয় বাঁশদহের মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে। স্থানীয় বাবুলিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে বৃত্তিসহ এন্ট্রাস পাস করার পর তিনি কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে এফএ ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু মওলানা আকরাম খাঁর প্রভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে তিনি পরীক্ষার পূর্বে কলেজ ত্যাগ করেন এবং ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে তিনি সাংবাদিকতায় চলে আসেন এবং ১৯২০ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কলকাতায় মুসলিম মালিকানাধীন অনেকগুলো দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো: মোহাম্মদী, নবযুগ, সেবক, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, The Musalman, খাদেম, সওগাত, সহচর, বুলবুল ও সাম্যবাদী।
বিশ শতকের মধ্যভাগে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। চিৎপ্রকর্ষের সাধনায় অর্জিত প্রজ্ঞাবলে উন্নতমানের জীবনী, নকশা, সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রভৃতি রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। দু শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের লেখক ওয়াজেদ আলীর জীবনকালে প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা খুবই কম। ছোট ও মাঝারি আকারের জীবনী, অনুবাদ ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর আটটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। সেগুলো হলো মরুভাস্কর, স্মার্ণানন্দিনী (অনুবাদ), ছোটদের হজরত মোহাম্মদ, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী, ডন কুইজসোটের গল্প, মহামানুষ মুহসিন ও সৈয়দ আহমদ। এগুলির মধ্যে মরুভাস্কর ও স্মার্ণানন্দিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি বাংলা একাডেমি থেকে তাঁর রচনাবলির অংশ বিশেষ দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ওয়াজেদ আলী প্রথম দিকে ইংরেজিতেও কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন।
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ছিলেন মুসলিম কৃষ্টি ও সমাজজীবনের একজন ব্যাখ্যাকার এবং একজন আদর্শবাদী সাহিত্যিক। তিনি সরকারি চাকরি পরিত্যাগ করে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে সমাজসেবাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম সমাজের নানা দোষত্রুটি, নতুন রাজনৈতিক পটভূমিতে সমাজ ও জীবন বিকাশের ধারা এবং ভাষা ও সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সমকালীন পত্র-পত্রিকায় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি যুক্তিবাদী মন ও পরিচ্ছন্ন চিন্তার অধিকারী ছিলেন। ১৯৫৪ সালের ৮ নভেম্বর স্বগ্রামেই তাঁর মৃত্যু হয়। সূত্র: বাংলাপিডিয়া
অল্পদিন হইল মুসলমান শিক্ষিতদের দৃষ্টি বাঙলা সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা এবং এই মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সেবা ব্যতীত আমাদের সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি একেবারে অসম্ভব। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের সেবা ক্ষেত্রে বর্তমান সময় নূতন করিয়া পদার্পণ করিয়াই মুসলমানেরা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য সমিতি গড়িয়া তুলিতে ব্ৰতী হইয়াছেন।
হিন্দুরা প্রশ্ন করেন, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের ন্যায় সাহিত্য–সেবা ক্ষেত্রে মুসলমানদের এই স্বাতন্ত্র্য কেন? হিন্দু ভ্রাতাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমরা এ বিষয়ে দুই চারটি কথা বলিতেছি।
প্রথমেই বলা উচিত যে, রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রের ন্যায় মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সেবার ব্যাপারেও যদি মুসলমানদিগকে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে না হইত, যদি হিন্দুদের সাহিত্য পরিষদের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গিয়া সাহিত্য সেবার পথে অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত ও সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের অপেক্ষা কেহ অধিক সুখী হইতেন না।
মুসলমানেরা সাহিত্য ক্ষেত্রে কতকটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পক্ষপাতী কেন–এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে কিঞ্চিত ‘গোড়ার কথা‘ বলিয়া লইতে হইবে।
সাহিত্য–সেবার উদ্দেশ্য কি? ‘নির্জলা‘ আর্ট ভক্তদের মতামত যাহাই হোক না কেন, যাঁহারা আর্টের উদ্দেশ্যহীনতা মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ, তাঁহারা বলিবেন যে, সমাজকে বর্তমান অপেক্ষা একটা বিরাটতর, উচ্চতর, মহত্তর, সুন্দরতর ভবিষ্যতের দিকে গতিশীল করিয়া দেওয়াই প্রকৃত সাহিত্য সাধনার লক্ষ্য। কিন্তু সে ভবিষ্যতের স্বরূপ কি? সাহিত্যশিল্পীদের নির্মিতব্য সে ভবিষ্যৎ সৌধের ভিত্তি কি? এক কথায় তাহার ভিত্তি হইতেছে জাতীয় বিশিষ্ট সভ্যতার সার্বজনীন উপকরণগুলি। ফলকথা, যে সমাজের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি হইবে, তাহার জ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষা ও কর্মসাধনার বিশ্বরূপকে সাহিত্যিক তাঁহার নিপুণ তুলিকার সাহায্যে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়া একটা মোহন সুন্দর আদর্শরূপে তাহার সম্মুখে ধরিবেন, ইহাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। যুগধর্মের প্ররোচনায় এবং অন্য সমাজ ও সভ্যতার সংস্পর্শে ও সংঘাতের ফলে কোন বিশিষ্ট সমাজের পক্ষে নব–নব রূপ ও রস গ্রহণ করা যতই বাঞ্ছনীয় হোক না কেন, তাহার বৈশিষ্ট্যকে সে কোন মতেই বিসর্জন দিতে পারে না, দিলে তাহাকে আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হইবে, যিনি যাহাই বলুন, কার্যতঃ কোন সমাজ অন্যের দ্বারা পরাজিত ও পরিপ্লাবিত হওয়ার পূর্বে স্বেচ্ছায় এ পাপে কখনও লিপ্ত হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। সুতরাং মুসলমান সমাজও যে অনুরূপ মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।
বর্তমানে বাঙলার মুসলমান সমাজকে দুইটি বিরাট বিসদৃশ সভ্যতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ ইউরোপীয় সভ্যতা, দ্বিতীয়তঃ ভারতের হিন্দু সভ্যতা। ইউরোপীয় সভ্যতার কয়েকটি বহিরঙ্গের সহিত ইসলামী সভ্যতার বিরোধ থাকিলেও অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, যে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ফলে ইউরোপ আজ বিশ্বজয়ী হইয়াছে, আরব বা ইসলামী সভ্যতাই সে বিষয়ে তাহার শিক্ষাগুরু। এ কথা ছাড়িয়া দিলেও বাঙলা সাহিত্যের সেবা ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত আমাদের তেমন প্রত্যক্ষ ও নিকট সংঘর্ষ বিদ্যমান নাই। পক্ষান্তরে হিন্দু সভ্যতার সহিত ইসলামী সভ্যতার বিন্দুমাত্রও মিল বা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দু সভ্যতার ভিত্তি হইতেছে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ, বহুযুগ পূর্ব হইতে এই বিশিষ্ট রূপেই হিন্দু সভ্যতা আমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছে। ইসলামী সভ্যতার স্বরূপ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধনপূর্বক এক অদ্বিতীয়, নিরাকার, সর্বগুণকর, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপাসনা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই ইসলামের উদ্ভব। ইসলাম জাতিভেদ স্বীকার করে না। প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভ্রাতা এবং সকল মানুষই এক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ইহাই কোরআনের ঘোষণা। এমন দুইটি পরস্পরবিরোধী সভ্যতার মধ্যে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সাংসারিক জীবন কর্মের সংঘর্ষ হইতেছে। সাহিত্য–সেবা ক্ষেত্রেও এই সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, এ জন্য মুসলমানকে আত্মরক্ষার জন্য পূর্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।
ইহা কাহারো অবিদিত নহে যে, হিন্দু–সেবিত বাঙলা সাহিত্য হিন্দু সভ্যতাকে ভিত্তি করিয়াই দণ্ডায়মান। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, পুনর্জন্মবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি তাহার রক্তে–মাংসে, অস্থি–মজ্জায় রহিয়াছে। মুসলমানকে নিজের সঙ্গী, সহচর ও দোসররূপে পাইবার আশায় হিন্দু কখনও বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গ হইতে তাঁহার নিজস্ব সভ্যতার এই ছাপগুলি তুলিয়া লইতে রাজী হইবেন না। পক্ষান্তরে মুসলমানও নিজের সার্বজনীন বিশিষ্টতাগুলি বিসর্জন দিয়া হিন্দু–সেবিত বাঙলা সাহিত্যকে নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিংবা হিন্দুর অন্ধ অনুকরণ দ্বারা নিজের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতে সম্মত হইবে না।
বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দুরা শ্রদ্ধা করেন, কারণ তিনি স্বদেশ মন্ত্রের পুরোহিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে কি দিয়া গিয়াছেন? তিনি যে স্বাদেশিকতার আদর্শ দান করিয়া গিয়াছেন, মোসলেম বিদ্বেষকেই তাহার ভিত্তি করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীত-‘বন্দে মাতরম্‘ গান পৌত্তলিকতার ভাবে পরিপূর্ণ, তাহা কোন অপৌত্তলিক–একেশ্বরবাদী নিজের ধর্ম বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। তথাপি হিন্দুরা এই সঙ্গীতটিকেই হিন্দু–মুসলমানের সম্মিলিত জাতীয় সঙ্গীতরূপে চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যাঁহারা অগ্নিমন্ত্রের সাধনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ঘোর পৌত্তলিকতার মধ্য দিয়ে মোসলেমহীন বাঙ্গালা বা ভারতের কল্পনা করিয়া নিজেদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। হিন্দু–সেবিত সাহিত্যের প্রভাব এইভাবে জাতীয় মনের উপর কার্য করিয়াছে। ইহাকে মুসলমানরা যুগপৎ ভয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক ।
বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত অসামান্য প্রতিভা হিন্দু সমাজ ও সভ্যতার অঙ্গ মাত্র। যেভাবে তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে এবং সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা ভিন্ন অন্যভাবে তাঁহার বিকাশ বা প্রকাশের উপায় ছিল না। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অসামান্য হইলেও তাহা সার্বজনীনতার সুউচ্চ গ্রামে আরোহণ করিতে পারে নাই ।
কিন্তু শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করিয়া লাভ নাই। প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু–সেবিত বঙ্গ সাহিত্য হিন্দু সভ্যতা হইতে রূপ–রস সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। পৌত্তলিক হিন্দু সভ্যতাকে ভিত্তি করিয়া, পৌত্তলিক সংস্কৃত–প্রাকৃত সাহিত্য হইতে জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিয়া, পৌত্তলিক হিন্দু মনের ছাপ সর্বাঙ্গে ভিতরে–বাহিরে ধারণ করিয়া এই সাহিত্য বিরাজমান। মোসলেম সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে ইহা মারাত্মক। মুসলমান ইহা বুঝিতে না পারিয়া একবার সর্বনাশের পথে উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব কবিদের কোমল মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের সুললিত পদাবলীর রূপ–রসে মজিয়া মুসলমান একবার নিজেকে হারাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব কবিতার সহজ সৌন্দর্যে কিছুকাল সম্মোহিত থাকিবার পর মুসলমান ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন প্রাচীন বাঙ্গলা বর্জনপূর্বক তাহার স্থানে দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত আমদানী করিলেন তখন মুসলমানদের চৈতন্য আরও অধিক পরিমাণে ফিরিয়া আসিল। হিন্দু রাজকন্যা সংস্কৃতার চেহারা দেখিয়া তাঁহারা একেবারে থতমত খাইয়া গেলেন। এই অবস্থা মোসলেম চিত্তে অতি শুভ প্রতিক্রিয়া করিল। তাঁহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর জাগ্রতভাবে নিজের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যের বিষক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা পূর্ব হইতেই বাঙ্গলার মুসলমানদের ব্যবহৃত আরবী–ফারসী শব্দ বহুলভাবে ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃতপ্রিয়তার ফলে তাঁহাদের এই চেষ্টা দ্রুততর হইয়া উঠিল।
ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয় কুমার প্রভৃতি প্রতিভাশালী সাহিত্যিক ও কবিগণ আবির্ভূত হইয়া যে সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, তাহাও স্বাভাবিকভাবে হিন্দু–সভ্যতার দ্বারা অন্তরে–বাহিরে অনুরঞ্জিত হইল। মুসলমানেরা কিছুদিন ইহা হইতে দূরে রহিলেন। কিন্তু সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শিক্ষিতেরা ক্রমশঃ এই সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। পুরাতন “মুসলমানী” বাঙ্গলা লিখিত কেতাব পুঁথি আর তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলাই শিক্ষণীয় বাঙ্গলা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। একদল মুসলমান লেখক এই অবস্থা সমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহারা পুরাতন বাঙ্গলা ছাড়িয়া দিয়া তথাকথিত ‘সাধু‘ বাঙ্গলায় সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও কয়েকজনের মধ্যে হিন্দু সাহিত্যের প্রভাব কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, শুধু ‘বিষাদ সিন্ধু‘ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির ভাষা ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা সহজে উপলব্ধি হইতে পারিবে।
তারপর এই বর্তমান যুগের বাঙ্গলা সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদিগের চেষ্টায় বাঙ্গলা ভাষা পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরল হইয়া আসিয়াছে। এজন্য এবং অন্যান্য কারণে শিক্ষিত মুসলমানেরা এখন বাঙ্গলার দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সাহিত্যের চর্চা করিতে আসিয়া তাঁহারা একটা অনাত্মীয় সঙ্কীর্ণ সভ্যতার বিষবাষ্পে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। তাই পূর্বযুগের সদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহারা আবার আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে নিজস্ব ধ্যান–ধারণা, চিন্তা–সাধনা, ভাব–প্রেরণা আনয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গলার মুসলমানদের নিজস্ব সভ্যতা ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ইহা ব্যতীত তাঁহাদের গত্যন্তর নাই ।
পুরাতনপন্থী পন্ডিতেরা এখনও মাঝে মাঝে হাঁকিয়া বলিতেছেন, যবন ম্লেচ্ছের সংস্পর্শ হইতে বাঙ্গলার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চল। বাঙ্গলা সাহিত্যের আদি যুগ হইতে মুসলমানদের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার ফলে তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইসলামের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সভ্যতার উত্তরাধিকারী পৌত্তলিক হিন্দুর অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সাহিত্য সেবা করিতে গেলেই তাঁহাকে বাগদেবী বীনাপানির রাতুল চরণে ভক্তি কুসুমাঞ্জলী উপহার দিতে হইবে। হিন্দু–সভ্যতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নহে—বর্তমান যুগে শিক্ষা–দীক্ষা, জ্ঞান–সাধনা ও তজ্জনিত শক্তি সামর্থ্যে বলীয়ান হওয়ায় হিন্দু–মানসিকতার সংক্রামণ অত্যন্ত ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার আওতায় গেলে মুসলমানের স্বরূপ লুপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে মুসলমানরা বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের বুকে তাঁহাদের নিজস্ব সভ্যতার জন্য স্থায়ী আসন রচনা করিতে চাহেন।
প্রকৃত দেশকল্যাণের দিক দিয়া চিন্তা করিলে ইহাতে হিন্দুদের অসন্তুষ্টির কোন কারণ থাকিবে না। হিন্দু মুসলমানকে এবং মুসলমান হিন্দুকে বুঝিতে না পারিলে, বুঝিয়া উভয়ের মধ্যে মৈত্রী বিধানের একটা পথ পরিষ্কার করিতে না পারিলে, এ দেশের কোন প্রকার স্থায়ী কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে না। উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত উদার ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিবে, তবেই উভয় সম্প্রদায় দেশের মঙ্গল সাধনে সমব্রতী হইতে পারিবে। সাহিত্যের ভিতর দিয়াই এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হওয়া সম্ভব।
কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে যদি মুসলমানেরা নিজস্ব ভাবধারা আমদানী করিতে না পারিল, তাহা হইলে হিন্দুরা তাহাদিগকে চিনিবেন, জানিবেন, বুঝিবেন কিরূপে? বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের মারফতে হিন্দুকে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে, কেননা মূলতঃ এবং প্রধানতঃ হিন্দুরাই সাহিত্যিক। মুসলমানকেও অতঃপর বাঙ্গলার মারফতে স্বকীয় স্বরূপ লোকচক্ষুর গোচরীভূত করিতে হইবে। যে ভাষা কেবলমাত্র হিন্দু চিন্তার বাহন, তাহা দ্বারা মুসলমানের সকল চিন্তা, সকল ভাব প্রকাশিত হইতে পারে না। এ জন্য মুসলমানদের ব্যবহৃত শব্দ অবাধে বাঙ্গলা ভাষায় গৃহীত হওয়া আবশ্যক। হিন্দু পন্ডিত ইহাতে নিশ্চয়ই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন, ঐ সকল স্লেচ্ছ ভাষার শব্দ বাঙ্গলায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রধানতঃ এই জন্যই হিন্দুর সহিত মুসলমানের বনিবনাও হইতেছে না। অবশ্য প্রয়োজন–অপ্রয়োজন বিবেচনা না করিয়া যথেচ্ছভাবে আরবী–ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হইলে তাহাতে আপত্তি করা অন্যায় নহে, কিন্তু যেখানে মুসলমানী পরিভাষার অর্থ ও সঙ্গতি রক্ষার জন্য এইরূপ শব্দ ব্যবহার করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, সেখানে কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দু ভ্রাতারা এতটুকুও মানতে রাজী নহেন।
দুঃখের বিষয়, মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যেও দুই–চারিজন আছেন, যাঁহারা মুসলমানদের সাহিত্য–সৃষ্টির প্রয়াসকে সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নিজের দৃষ্টি এতই সঙ্কীর্ণ অথবা স্বজাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান এতই অল্প যে, পরের কুযুক্তিকে তাহারা সহজেই পরম সুযুক্তি বলিয়া মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন। তাহারা ভুলিয়া যান যে, হিন্দুরা মুখে যত বড় বড় কথা বলুন না কেন, কার্যতঃ তাহারা হিন্দু সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্য গঠন করিয়াছেন ও করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া চুনাপুটি সাহিত্যিক পর্যন্ত কেহই বাঙ্গলা সাহিত্যে হিন্দু সভ্যতাকে বর্জন করিতে ইচ্ছুক নহেন। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সভ্যতার জয়–গৌরব ঘোষণার জন্য বৃহত্তর ভারত আবিষ্কারের কল্পনায় অধীর হইয়া এই বৃদ্ধ বয়সেও সাগর পাড়ি দিতে ত্রুটি করিতেছেন না। ইহাতে যদি তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ না পায়, তবে মুসলমান বেচারারা তাঁহাদের সভ্যতার ছাপ বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গে লাগাইয়া দিতে চাহিলে, তাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলা হইবে কেন? পরলোকগত গিরিশচন্দ্র সেন ভিন্ন অন্য কোন খ্যাতনামা হিন্দু বা ব্রহ্ম সাহিত্যিক এ যাবৎ ইসলামী সভ্যতাকে ভালরূপে জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। কেবল হিন্দু সভ্যতা লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত। ইহাতে যদি তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ না পাইয়া থাকে, তবে নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি প্রয়াসী মুসলমানদিগকে সঙ্কীর্ণদৃষ্টি বলা হইবে কোন অপরাধে ?
যে সুযোগের অভাবে বাঙ্গালী হিন্দুদের সহিত আমাদের প্রকৃত পরিচয় হইতেছে না, আমরা ইচ্ছা করিলেই যখন তাহাদিগকে সে সুযোগ করিয়া দিতে পারি, তখন আমরা তাহা করিব না কেন? হিন্দুরা যেমন বাঙ্গলা সাহিত্যের মারফতে তাঁহাদের সভ্যতার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইতেছেন, আমরা মুসলমান সাহিত্যিকরাও তেমনিই ইসলামী সভ্যতার উপকরণগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যের মারফতে হিন্দুদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। তাহা না করিলে আমাদিগকে কর্তব্যদ্রষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় মুসলমানী সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা কোন মতেই নিন্দার পাত্র নহেন; বরং সর্বদা প্রশংসা পাইবার অধিকারী।
আমরা নানা কারণে স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গলা সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইলেও একটি বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। বর্তমান যুগের হিন্দু–সেবিত সাহিত্যের ভাষা ও আমাদের ভাষায় যাহাতে গুরুতর রকমের পার্থক্য না ঘটে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কেননা, ঐ রূপ বৃহৎ পার্থক্য ঘটিলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। আমরা আবশ্যক মত আরবী–ফারসী শব্দ ব্যবহার করিব কিন্তু এইরূপ শব্দ ব্যবহারে যেন আমাদের অতি লোভ না জন্মে। আমাদের এরূপ সাহিত্য সৃষ্টির নামে একেবারে “আমির হামজা” বা “ছহি বড় সোনাভান” বা “শূর্য্য উজ্জ্বল বিবির কেচ্ছা” রচনা করা কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অবশ্য আমাদের সমাজে দুই–একজন লোক এমন আছেন যাঁহারা কোন ব্যক্তিকে ” দয়ার পাত্র” মনে না করিয়া “কাবেলে রহম” মনে করিলে ইসলামী ভাব প্রকাশ পাইল বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা নিজেরাই দয়ার পাত্র এবং বড়ই সুখের বিষয়, ইহাদের সংখ্যা, প্রতিপত্তি ও সাহিত্যিক যোগ্যতা নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য। আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যে ইসলামী ভাব আনয়ন করিতে যতই উৎসুক হই না কেন, এইরূপ উৎকট মনোভাব বর্জন না করিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। পক্ষান্তরে মুসলমানদের নিত্যব্যবহার্য নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, কেবলা, জায়নামাজ, আল্লাহ্, রাসূল, পীর, ওলি, ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, বেদাৎ প্রভৃতি শত শত ইসলামী পারিভাষিক শব্দ কোন মতেই বর্জন করা যাইতে পারিবে না। কেননা বাঙ্গলা ভাষায় ঐ সকল শব্দের অনুবাদ হওয়া অসম্ভব। এইভাবে উভয় দিক বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি কোরআন। ইহার নিম্নে বিশ্বস্ত হাদিসের স্থান। তারপর ফেকা, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা–প্রশাখা। ইসলামের এই সকল উৎস হইতে ভাবধারা সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করিতে হইবে। তবেই আমাদের সাহিত্য সাধনা সফল ও সার্থক হইবে।
প্রশ্ন হইতে পারে, মুসলমান ও হিন্দু যদি এইভাবে পৃথক সাহিত্য চর্চায় ব্যাপৃত হয়, তবে সাহিত্য–ক্ষেত্রে উভয়ের মিলন কবে হইবে, কিরূপে হইবে? আমাদের মনে হয়, এ যাবৎ মুসলমানেরা যেমন হিন্দুদের ভাব ও চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, মুসলমানদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহতগতিতে চলিলে অল্পকাল পরেই হিন্দুরা তেমনিই মুসলমানদের নিজস্ব ভাব ও চিন্তার সহিত পরিচয় লাভ করিবেন। এই সময় হইতে উভয় সম্প্রদায় একযোগে সমবেত শক্তি প্রয়োগে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পরিচর্যা করিতে পারিবেন।
মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে সাহিত্য–সেবকের সংখ্যা—শক্তিশালী সাহিত্য–সেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। হিন্দু ভ্রাতারাও ক্রমে ক্রমে মোসলেম–সেবিত সাহিত্যের প্রতি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইবেন। ইহার ফলে পণ্ডিতদিগের প্রভাব–প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবে। বাঙ্গলায় এক শক্তিশালী সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে।
[অগ্রপথিক, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ সংখ্যার সৌজন্যে। যোগাযোগ–এর পাঠকদের জন্য রচনাটি পুনরায় প্রকাশ করা হলো। লেখকের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।—সম্পাদক।]



সুন্দর লিখেছেন লেখক।
দারুণ কনসেপ্ট!